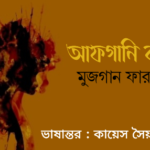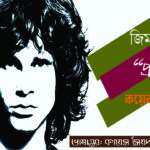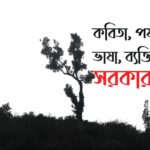এজরা পাউন্ড এর জীবন ও কর্ম ।। ক্লাইভ উইলমার, অনুবাদ- জয়ন্ত বিশ্বাস
পাউন্ডের জন্ম ইডাহো (Idaho)-র হেইলি (Hailey)-তে হলেও তাঁর বেড়ে ওঠা ও শিক্ষাজীবন কাটে মূলত পেনসিলভানিয়া (Pennsylvania)-য়।
স্বল্পায়ু শিক্ষাজীবনের পাট চুকিয়ে ১৯০৮ সালেই পাউন্ড ইউরোপে পাড়ি জমান। কয়েক মাস ভেনিসে কাটাবার পরে তিনি শেষ পর্যন্ত লন্ডন-এ থিতু হন। এখানেই পাউন্ডের সাথে তাঁর আশৈশব নায়ক ডাব্লিউ বি ইয়েটস (W.B. Yeats)-এর সখ্যতা গড়ে ওঠে। ১৯০৮ থেকে ১৯১১ সালের মধ্যে তাঁর ছয়টি কাব্যসমগ্র প্রকাশিত হয়। এগুলোর অধিকাংশেই Provençal বা ফ্রান্সের প্রঁভাস প্রদেশের লোককথা এবং পূর্ববর্তী ইতালিয়ান কবিতার প্রভাব, তথা কবির অনুরাগ ফুটে উঠেছিল। তাঁর রচনারীতি আরও শানিত হয় ব্রাউনিং (Browning) এর মধ্যযুগীয় ধাঁচ এবং প্রাক-রাফায়েলীয় (Pre-Raphaelites) রীতি ব্যাবহারের মধ্য দিয়ে। মূলত ফোর্ড ম্যাডক্স ফোর্ড (Ford Madox Ford) এবং হিউম (T. E. Hulme) এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েই পাউন্ডের লেখনী আধুনিকতাবাদের দিকে ঝুঁকতে থাকে। ১৯১২ সালে পাউন্ড বিখ্যাত ‘Imagist movement’ এর ভিত্তিমূল গড়ে তোলেন। তিনি এর মাধ্যমে মূর্ততা, সংক্ষিপ্ততা আর মুক্তছন্দ-কে সমর্থন জানান। ‘In a Station of the Metro’ এর মত তাঁর রচিত সংক্ষিপ্তাকার কিছু Imagist কথকতায় প্রাচ্যদেশীয় মৃদুতা স্পষ্ট হয়। এটিই পরবর্তীকালে ‘Vorticism’ (সমসাময়িক চিত্রকলাভিত্তিক সাংস্কৃতিক ধারা) এর আনুষঙ্গিক, গতিময় নব্য (avant-garde) বৈশিষ্ট্য লালন করে চলে। Vorticist চিত্রশিল্পী যেমন হেনরি গ্যঁদিয়ে-ব্রেয্কা (Henri Gaudier-Brzeska), ওয়াইন্ডহ্যাম লুইস (Wyndham Lewis) প্রমুখের সাহচর্য পাউন্ড লাভ করেছিলেন। তাঁদের সহায়তাতেই পাউন্ড কবিতার গঠনে ‘বিপরীতধর্মিতা’ (যা মূলত Post-Cubist ভাস্কর্যে প্রতীয়মান) ব্যাবহারের অনন্য পন্থাটি আবিষ্কার করেন। এই পদ্ধতি প্রায়োগিকভাবে তিনি ব্যাবহার করেন আর্নেস্ট ফেনোওয়া (Ernest Fenollosa) অনূদিত ক্লাসিক চীনা কাব্যসংকলন সংক্রান্ত কাজে। এই সংকলন তাঁর হাতেই পরিণতি লাভ করে Cathay (1915) নামক অসাধারণ এক মুক্তছান্দিক চেহারায়।
অবশ্য ফেনোওয়া এর বিপরীতে যুক্তি দিয়েছিলেন যে চীনা ভাষার লিখিত অক্ষরসমূহ বস্তুত প্রতীকীভাবে ব্যাবহৃত হয়, অর্থাৎ সংক্ষেপণ ও বিমূর্ততা ‘দৃশ্যমান রূপক’(visual metaphors)-র সাথে জড়িত থাকে। এইসব দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রতীকসমূহের পারস্পরিক ওতপ্রোততার ভিতরেই পাউন্ড কবিতার এক নতুন গঠনরীতি আবিষ্কার করে বসেন। এই নতুন কাঠামো গতিময়তা আর সংক্ষিপ্ততার গুণে ঋদ্ধ। এর পাশাপাশি এই কাঠামো চিত্রকল্পই শুধু নয়, কাব্যিক উপাদান যেমন – allusions, quotations, fragments of narrative – এগুলোরও বিসদৃশে অবস্থান নেয়।
পাউন্ডের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য কাজ ‘The Cantos’ (1915) এ-ও এই কাঠামোরীতি প্রয়োগ করার চেষ্টা লক্ষ্যণীয়। এখানে অন্য ভাষা থেকে উদ্ধৃতি তো বটেই, এমনকি গদ্য থেকে নেওয়া বাক্যাংশ পর্যন্ত ব্যাবহার করা হয়েছে। শিল্প-সংস্কৃতির অঙ্গনে পাউন্ডের যে ব্যক্তিগত মেধার পাল্লা, সেটির তাগিদেই তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে নব্য রেনেসাঁর কেন্দ্র হতে যাচ্ছে নিঃসন্দেহে লন্ডন। এখানে তাঁর ভূমিকা হয়ে ওঠে একাধারে একজন পৃষ্টপোষক, একজন সম্পাদক এবং একজন মুখপাত্রের। ইয়েটস-এর পরিপক্ক লেখনশৈলীর পিছনে অবদান রাখা থেকে শুরু করে জয়েস, এলিয়ট প্রমুখের কাজের মর্মার্থ উপলব্ধি ও প্রচারণা, এমনকি লন্ডনের এক ‘মডার্ন আর্ট ‘ খরিদের জন্য জনৈক মার্কিনী ব্যবসায়ীকে পরামর্শদান, প্রত্যেকটি জায়গা ছিল পাউন্ডের একক পদচারণায় ভারাক্রান্ত। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অকস্মাৎ অনুপ্রবেশের দরুন তাঁর আশা-ভরসা একরকম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর জীবনের পরবর্তী কাজগুলোর উপরে এই নৈরাশ্যের ছায়া পড়ে এবং নিদারুণভাবে প্রভাবিতও করে। তাৎক্ষনিকভাবে বিচার করতে গেলে তাঁর প্রথম দিকের গুরুত্বপূর্ণ কাব্যসমূহ যেমন ‘Homage to Sextus Propertius (১৯১৯) ও Hugh Selwyn Mauberley (১৯২১) এই নৈরাশ্যের উৎসমূল থেকেই উদ্ভূত হয়েছে।
এই দুইটি প্রহসনমূলক অনুক্রমিক কবিতার ভিতরেও দ্বান্দ্বিকতা লক্ষ্যনীয়। মুক্তগদ্যছন্দে লেখা ‘Homage’-এ একধরনের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের অস্তিত্ব দেখা যায়। এটি মূলত প্রথম শতাব্দীর রোমান কবিতার ভাষা অবলম্বনে লেখা। এর উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধের সাথে উঠে আসা সাম্রাজ্যবাদী উগ্র দেশপ্রেমের (imperialistic jingoism) বিপরীতে কাব্যের অন্তর্নিহিত ব্যক্তিস্বাধীনতা ও প্রেম বা কামমূলক বৈশিষ্ট্যাদি রক্ষা করা। অন্যদিকে ‘Mauberly’-তে একটি আঁটসাঁট ছন্দমিল বজায় রেখে ব্যঙ্গাত্মক স্তবকের অবতারণা ঘটানো হয়েছে। এখানে যুদ্ধকে বলা হয়েছে হীনবীর্য ও সংকীর্ণমনা সংস্কৃতি থেকে উদ্ভূত ‘Götterdammerung’। এখানে নিজের গণ্ডিবদ্ধতাকে স্বীকার করে নেওয়ার জন্য পাউন্ড একে তীব্র ভাষায় দোষারোপ করেছেন।
তাছাড়াও এই কবিতাগুলো কাজের সুবাদে এলিয়টের সাথে পাউন্ডের নিবিড় সম্পর্কেরও বড় সাক্ষ্য বহন করে। কেননা এখানে এলিয়টের রুচি বেশ সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে ( সমসাময়িক ‘Sweeney’ শীর্ষক কবিতাগুচ্ছ)। তাঁদের সম্পর্ক চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে, যখন এলিয়ট তাঁর ‘Waste Land’ (১৯২২) পরিমার্জনের জন্য পাউন্ডের বিশ্বস্ত হাতেই তুলে দেন। এরই সাথে সাহিত্যের ইতিহাস আলাদা একটি মাত্রা লাভ করে।
‘Mauberley’- কে ধরা হয়ে পাউন্ডের জানানো লন্ডনের প্রতি বিদায় সম্ভাষণ। ১৯২০ সালে তিনি লন্ডন ত্যাগ করে প্যারিস যাত্রা করেন। সেখানে চার বছর অতিবাহিত করার পরে তিনি আবারও রওনা দেন ইতালি অভিমুখে। ইতালিতে তিনি আস্তানা গাঁড়েন রাপালো (Rapallo) তে। সময়টা তখন ১৯২৪। তিনি এবারে ‘The Cantos’ রচনায় মনোনিবেশ করেন। এই ‘ইতিহাস ঘিরে থাকা কবিতা’-র প্রথম খণ্ড ১৯২৫ সালে প্রকাশিত হয়।
The Cantos বিবেচনা করলে স্পষ্টত বোঝা যায়, পাউন্ড অর্থনীতি বিষয়ক চিন্তাভাবনায় বেশ জড়িয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী, যুদ্ধ নামক বিষয়টির উৎপত্তি ঘটেছিল আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদীদের প্রতিযোগিতা, বা শত্রুতার রেশ ধরে।
তিনি নিজে মনে করেছিলেন, লাগামছাড়া এই পুঁজিবাদের যে ভয়াবহ প্রকোপ, সেটির একটি জুতসই সমাধান তিনি খুঁজে পেয়েছেন। এটি ছিল মেজর ডগলাসের (Major C. H. Douglas) ‘সামাজিক আমানত তত্ত্ব’ (Social Credit theory), যা কিনা শিল্পকলা বা নন্দনতত্ত্বের অনুকূলে অবস্থান নেয়। ডগলাসের মতে, একটি ভূখন্ডের আমানত লেনদেন ব্যবস্থার পক্ষে উচিৎ হবে আপামর জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির পক্ষে কাজ করা। এর মাধ্যমে সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটবে এবং ব্যাংকার ও অর্থলগ্নিকারীদেরও ক্ষমতা কুক্ষিগত করার সুযোগ থাকবে না। ইতালির ফ্যাসিবাদী নেতা মুসোলিনীর (Mussolini) তারুণ্যদীপ্ত বক্তব্য ও অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রতিশ্রুতি শুনে তাঁর প্রতি পাউন্ডের মুগ্ধতা জন্মে। পাউন্ড অকপটেই বিশ্বাস করে নিয়েছিলেন যে মুসোলিনী হয়ত ডগলাসের তত্ত্বটিকে কার্যকর করবেন।
প্রথমত, পাউন্ড ‘usury’ (মহাজনী/সুদবৃত্তি) নামক সৃজনশক্তি বিনষ্টকারী একটি অতিপ্রাকৃত সত্ত্বা কল্পনা করে নেন (Canto 45) এবং সেটিকে উদ্দেশ্য করে লিখিত আক্রমন চালাতে থাকেন। ১৯৩০ নাগাদ তিনি প্রধানত ইহুদীদেরকে এই ‘মহাজন’ বা ‘সুদখোর’ হিসাবে উল্লেখ করেন। এই সময়ে তাঁর ভাষাও উগ্র অ্যান্টি-সেমিটিজম (Anti-Semitism) দোষে বিকৃততর হতে থাকে।
XXX Cantos (১৯৩০) এর এক খসড়াতে কবিকে দেখানো হয় মৃতদের মধ্যে ইতস্তত ভ্রাম্যমাণ ওডিসিয়াস (Odysseus) রূপে। ‘সন্নিধি’ (juxtaposition)-র ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি ইতিহাসের আবর্তিত ছাঁচটিকে উন্মুক্ত করেন। এছাড়াও সময় দ্বারা সন্নিবেশিত অভিজ্ঞতালব্ধ জগৎকে তিনি বিনির্মাণ করেন দেবদেবীদের আবাস স্বরূপ এক শাশ্বত জগৎ হিসাবে। প্রথম ৩০টি Cantos এর ভূমধ্যসাগরীয় (Mediterranean) ভাবধারার প্রভাববলয় থেকে বের হয়ে পরবর্তীগুলো (Cantos 31-70,প্রকাশ ১৯৩৪-৪০) পূর্বতন মার্কিন রাষ্ট্রপতিগন ও প্রাচীন চীনের অর্থনৈতিক পন্থাকেও তুলে নিয়ে আসে। গতানুগতিক নীতিশিক্ষামূলক বৈশিষ্ট্য ও রসস্ফীতি থাকা সত্ত্বেও এই অংশে পাউন্ডের শ্রেষ্ঠতম কিছু কাব্য (যেমন Cantos 36,45, 47, এবং 49) স্থান পেয়েছে।
১৯৩০ সালের পরবর্তী সময়ে পাউন্ড তাঁর উদ্যমের অনেকটাই ব্যয় করেন ফ্যাসিবাদের (Fascism) সমর্থন জোগানো এবং সম্ভাব্য যুদ্ধ প্রতিহত করার চেষ্টায়। যখন যুদ্ধ শুরু হয়, তিনি মার্কিন ছত্রীসেনাদের উদ্দেশ্যে উন্মত্তের মত বাক্যবাণ বর্ষণ করেন; সেগুলো আবার রোম রেডিও থেকে সম্প্রচারও করা হয়। এর ফলশ্রুতিতে ১৯৪৫ সালে স্বপক্ষভুক্তদের হাতে তিনি গ্রেফতার হন। তাঁকে মার্কিন সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। তাঁকে ৬ মাস পিসা (Pisa) -র কাছাকাছি এক নিয়মশৃঙখলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অন্তরীন রাখা হয়। একই সময়ে তাঁর উপরে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য বিচারকার্যের প্রস্তুতি চলতে থাকে। অনুমান করা হয় যে, প্রথম ৩ মাসের অমানুষিক অভিজ্ঞতা সহ্য করে তাঁর যৌক্তিকতাবোধ বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ইতোমধ্যে তাঁর লেখাতেও এই মানসিক বিকারগ্রস্ততার একটা ছাপ লক্ষ্যণীয় ছিল। বিচারকার্যের সময় মানসিক অসুস্থতার কারনে তাঁকে বিচারপ্রার্থনার জন্য অনুপযুক্ত বলে রায় দেওয়া হয়। উপরন্তু তাঁকে ওয়াশিংটন ডিসি তে (Washington DC) সেন্ট এলিজাবেথ’স হাসপাতালে (St Elizabeth’s Hospital) ১৯৪৬ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত চিকিৎসাধীন রাখা হয়।
এই বন্দিত্ব পাউন্ডের মধ্যে এক শৈল্পিক উত্থান নিয়ে আসে। DTC তে থাকাকালীন খসড়াকৃত The Pisan Cantos (১৯৪৮) তাঁর লেখা সর্বাপেক্ষা ব্যক্তিগত কিছু কবিতার সংকলন। ইউরোপে ঘটে যাওয়া ট্রাজেডি সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন অবস্থাতেই তিনি সেই পটভূমিতে নিজের অতীত, বিশেষ করে জলরঙে আঁকা সেই আধুনিকতাবাদ আন্দোলনের (Modern Movement) কথা চিন্তা করেন। এই ধ্যান থেকেই কালজয়ী সৃষ্টিটির উদ্ভব।
তীব্র কষ্টভোগ আর অতীতচারণ, এই দুইয়ে মিলে তাঁর ভিতরে এক নব নম্রতার উন্মেষ ঘটায়। এর উদাহরণ পাওয়া যায় পারিপার্শ্বিকের প্রতি, যেমন – কীটপতঙ্গ, প্রানী, ক্যাম্প প্রহরী ইত্যাদিদের প্রতি তাঁর মমত্ববোধ অবলোকন করে। সেন্ট এলিজাবেথ’স-এ থাকাকালীন সময়েই তিনি আরও দুইটি দুর্বোধ্য কাব্যাংশঃ Rock-Drill (১৯৫৫) ও Thrones (১৯৫৯) এবং কনফুসিয়ান (Confucian) ক্ল্যাসিকস থেকে কিছু অনুবাদের কাজও সম্পন্ন করেন।
মুক্তি পাবার পরে পাউন্ড ইতালিতে ফিরে আসেন। ১৯৭২ সালে ভেনিস (Venice) শহরে তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে। শেষ বছরগুলোতেও তাঁর মধ্যে প্রকাশ্য অবাধ্যতার লক্ষণ দেখা যায়। তবে এর পরেও এই সময়গুলো অনেকটাই ম্লান হয়েছে তাঁর আত্ম-দ্বন্দ্ব এবং ‘ত্রুটি ও ধ্বংস’ (errors and wrecks) বিষয়ক সচেতনতার উপস্থিতির কারনে। জনসম্মুখে খুব স্বল্পসংখ্যকবার উপস্থিত হয়ে তিনি তাঁর The Cantos রচনাটিকে ব্যর্থ বলে আখ্যা দেন। যদিও এই চিন্তা তিনি শেষ পর্যন্ত আঁকড়ে ধরে রেখেছিলেন কিনা, সেটা পরিষ্কার নয়, তবে এই কাব্য লেখা তিনি কখনোই সম্পূর্ণ করেননি। ১৯৬৯ সালে তিনি Drafts and Fragments of Cantos CX-CXVII নামক ৩২ পৃষ্ঠার কাব্যসংকলন প্রকাশ করে এটির ইতি ঘোষনা করেন। এর অধিকাংশই অক্ষুব্ধ ভাষায় লেখা হলেও এর খন্ডকাব্যগুলো ভাষার দিক দিয়ে ছিল যথেষ্ট শানিত।
এজরা পাউন্ড ছিলেন আধুনিকতাবাদ আন্দোলনের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব। ১৯১০ এর দিকে ইংরেজি কবিতায় নতুনত্ব নিয়ে আসার পিছনে কৃতিত্বের তিনিই ব্যক্তিগত দাবীদার। তবে তিনি একজন বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব হিসাবেই ইতিহাসের পাতায় রয়ে গিয়েছেন। রাজনীতির সাথে সংশ্রব শিল্প আর সভ্যতার প্রতি তাঁর মহৎ অবদানের পথকে কণ্টকিত করেছে। তাঁর সম্পর্কে সমালোচনাও কম হয় নি। অভিজাততন্ত্রী (élitist), দুর্বোধ্যতাস্রষ্টা (obscurantist), বাগাড়ম্বরপূর্ণ (charlatan)- কত নামেই তিনি পরিচিত। এরকমও কম বলা হয় নি, যে নিজের সৃষ্টি করা ‘avant-gardiste’ এর জাঁমজঁমকের বাইরে আধুনিক পৃথিবী সম্পর্কে কোন ধারণাই তিনি রাখেন না।
তবে এসবের কোনটাই তাঁর অর্জনের যে মূল, সেটিকে বিন্দুমাত্র স্থানচ্যুত করতে পারে নি। কেননা, মৌলিকভাবে ধরতে গেলে কলাকৌশলগত অর্জন যে জায়গায় অবস্থান নেয়, সেখানে দক্ষতার উন্নতিকল্প ক্রমশ একটি মানবীয় গুণে রূপান্তরিত হতে থাকে। তাঁর কাব্যিক আন্দোলনের সংবেদনশীলতার মাত্রাটিও ভিন্নতর।
এর মাধ্যমে মনে হয় যেন প্রতিটি বিষয়বস্তুকেই স্বাধীন এবং পৃথক ভাবে জীবন্তরূপে উপস্থাপন করা হচ্ছে। মনে হতে পারে যেন এসকল বিষয়বস্তু আদৌ সচেতনভাবে বাছাই করা হয় নি; অকস্মাৎ আবিষ্কৃত হয়েছে। সেটা অলিভ পাতা আন্দোলনের (Movement of Olive Leaves) পিছনে ইন্ধন জোগাতে হোক, অথবা রেনেসাঁ-কালীন কোন মার্সেনারি সৈনিকদলের দলপতির (Renaissance condottiere) চরিত্র অংকনেই হোক না কেন। এই সময়ের জন্যে উদ্ভাবিত অনুবাদকর্মের পিছনেও পাউন্ডের সমান দক্ষতা ও প্রতিভার ছাপ প্রতীয়মান। তিনি মূল লেখনীর নির্যাস বজায় রেখে একটি ভাষা সৃজন করতে পারতেন। আমাদের চেনা পৃথিবী থেকে দূরে হুবহু লিখিত বিবরণের মাধ্যমে একজন লেখকের দূরত্ব উপলব্ধি করানো, আবার একই সময়ে নিজের কাজটিকে আমাদের কাছে সহজগম্য করে তোলা, এই দুইয়েই তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। পাউন্ডকে যদি দুর্বোধ্যতার জন্য অভিযুক্ত করা হয়, তাহলে বলতে হয়, তাঁর কাজে রেফারেন্সের ব্যপক উপস্থিতির কারনেই সাধারণ পাঠকের কাছে এরকমটা মনে হয়। তিনি একজন শিক্ষাবিদ হিসাবেও অনন্য ভূমিকা রেখেছেন। কবিতার অন্তঃপুরে অবগাহনের মধ্যে দিয়েই পাঠক এক গুপ্তজগতের সন্ধান পেতেন। এই জগতটি পাউন্ডের অসীম মমতায় তিলে তিলে গড়ে তোলা, যার প্রতিটি প্রান্ত জুড়ে রয়েছে একান্তই তাঁর নিজের জন্যে উদ্ভাবিত বিদগ্ধ কার্যাবলী আর পরিকল্পনাসমূহের সমাহার। তাঁর এই মহৎ ব্রতের মর্মমূলে প্রবেশের সক্ষমতা যে সাধারণ পাঠকদের হয় নি, এর জন্যে পাউন্ডকে দোষারোপ করাটা নিতান্তই অবিচার হয়ে দাঁড়াবে।
From The Oxford Companion to Twentieth-century Poetry in English. Copyright © 1994 by Oxford University Press.